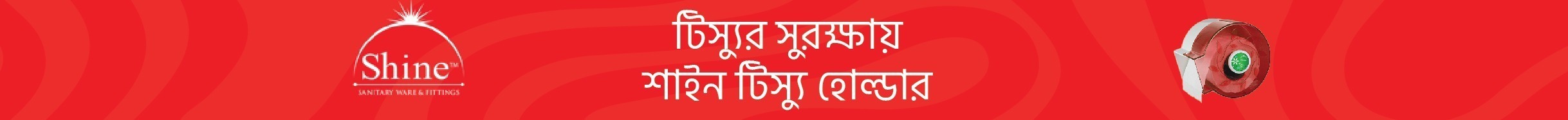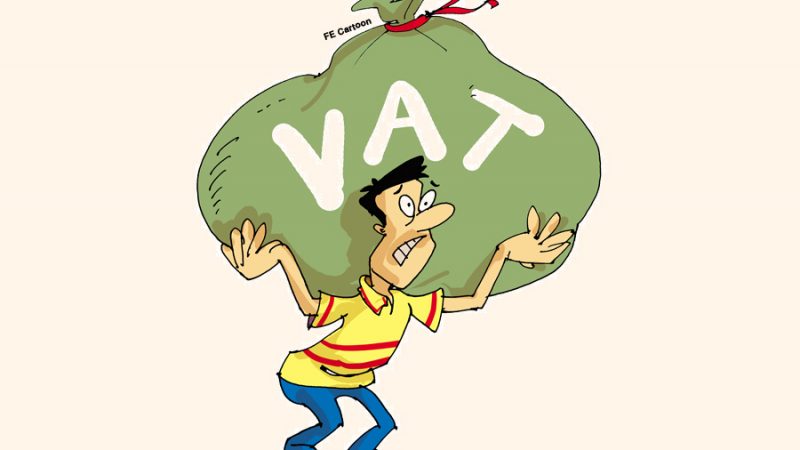ইনফ্লেশন ও ডিফ্লেশন কি? কিভাবে কাজ করে?

আপনারা অবশ্যই খেয়াল করে থাকবেন আজ থেকে ১০ বছর আগে ৫০ টাকায় যে পণ্য কেনা যেত, এখন তার বিনিময়মূল্য অনেক বেড়ে গিয়েছে। এর কারন কি? এমনটা হওয়ার কারন হলো ইনফ্লেশন। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাবধানে পণ্য ও সেবার বিনিময়মূল্য বেড়ে যাওয়াই হলো ইনফ্লেশন।
সহজ ভাষায় ইনফ্লেশন বলতে বোঝায় বাজারে সব কিছুর দাম ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়া। অর্থাৎ, একই পরিমাণ টাকা দিয়ে আগের চেয়ে কম পণ্য ও সেবা কেনা যায়। এটি মূলত অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
ইনফ্লেশন দুই ধরনের হয়ে থাকে। ডিমান্ড-পুল ইনফ্লেশন এবং কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন।
মনে করুন, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় ১০০ জন মানুষ আছে, আর সেই এলাকায় চালের চাহিদা খুব বেশি। কিন্তু বাজারে চালের পরিমাণ কম। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই চালের দাম বেড়ে যাবে, কারণ অনেকেই কিনতে চাইবে, কিন্তু চালের যোগান কম। এই অবস্থাকে বলে ডিমান্ড-পুল ইনফ্লেশন।
আবার মনে করুন, তেলের দাম বেড়ে গেল, ফলে পরিবহন খরচ বেড়ে গেল, যা উৎপাদন খরচও বাড়িয়ে দিল। এর ফলে বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। একে বলে কস্ট-পুশ ইনফ্লেশন।
এবং আরেকটি কারণ হলো, যখন কর্মীরা বেতন বাড়ানোর দাবি জানায় এবং প্রতিষ্ঠানগুলো সেই বেতন বাড়িয়ে দেয়। এতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়, ফলে পণ্যের দামও বাড়ে। একে বলে ওয়েজ-প্রাইস স্পাইরাল।
ইনফ্লেশনের ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়াকে বলে ডিফ্লেশন। অর্থাৎ, যখন বাজারে পণ্যের দাম কমতে থাকে। শুনতে ভালো লাগলেও এটি অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কারন, যদি মানুষ ভবিষ্যতে দাম আরও কমবে বলে ধরে নিয়ে কেনাকাটা কমিয়ে দেয়, তাহলে বাজারে পণ্য বিক্রি কমে যায়। এতে ব্যবসাগুলোর ক্ষতি হতে থাকে, নতুন বিনিয়োগ কমে যায়, কর্মসংস্থান কমতে থাকে, আর বেকারত্ব বাড়তে থাকে।
১৯৩০ সালের “গ্রেট ডিপ্রেশন” ছিল ডিফ্লেশনের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাজারে পণ্যের দাম ব্যাপকভাবে কমে গিয়েছিল। যার ফলে অনেক কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বহু মানুষ চাকরি হারিয়েছিল, আর অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।
অনেকেই ভাবেন ইনফ্লেশন মানেই হয়তো খারাপ কিছু। কিন্তু আসলে তা পুরোপুরি সত্য নয়। যদি ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় থাকে, তাহলে এটা অর্থনীতির জন্য ভালো হতে পারে। সাধারণত, বছরে ২-৩% ইনফ্লেশন স্বাভাবিক এবং সুস্থ অর্থনীতির লক্ষণ। উন্নয়নশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে, উচ্চ প্রবৃদ্ধির কারণে ৩-৫% পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতি স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে বাজারে প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ে, মানুষ বেশি খরচ করতে আগ্রহী হয়, আর কোম্পানিগুলো নতুন বিনিয়োগ করতে পারে।
কিন্তু সমস্যা হয় যখন ইনফ্লেশন মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়, যাকে হাই ইনফ্লেশন বা হাইপারইনফ্লেশন বলা হয়। হাইপারইনফ্লেশন মানুষের সঞ্চয় ও ক্রয়ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এই অবস্থায় জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যায়। পণ্যের দাম এত দ্রুত বাড়তে থাকে যে মানুষের আয় তার সাথে তাল মিলাতে পারে না। এমনকি চরম অবস্থায়, মুদ্রার মূল্য এত কমে যায় যে মানুষের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কেনাও কঠিন হয়ে পড়ে।
এর একটি উদাহরণ হলো জিম্বাবুয়ে, যেখানে ২০০৮ সালে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ হাইপারইনফ্লেশন হয়েছিল। সে সময় জিম্বাবুয়ের মুদ্রার মূল্য এতটাই কমে গিয়েছিল যে ১ কেজি চাল কিনতে ১০০ ট্রিলিয়ন জিম্বাবুয়ে ডলার লাগত!
মানুষ বেতনের টাকা পাওয়ার সাথে সাথেই ছুটে যেত বাজারে, কারণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ হয়ে যেত। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে সরকার ১০০ ট্রিলিয়ন ডলারের নোট ছাপাতে বাধ্য হয়। শেষ পর্যন্ত, জিম্বাবুয়েকে তাদের নিজস্ব মুদ্রা বাদ দিয়ে মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রা ব্যবহার করতে বাধ্য হতে হয়।
আরেকটি উদাহরণ জার্মানির হাইপারইনফ্লেশন। ১৯২৩ সালে জার্মানিতে এক টুকরা রুটি কিনতে লক্ষ লক্ষ জার্মানি মুদ্রা লাগত।
তাই, একটি সুস্থ অর্থনীতির জন্য নিয়ন্ত্রিত ইনফ্লেশন প্রয়োজন, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত ইনফ্লেশন বিপজ্জনক। এজন্য সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতির মাধ্যমে ইনফ্লেশনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, যেন এটি মানুষের জীবনযাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।
ইনফ্লেশন ও ডিফ্লেশন, দুটোই অর্থনীতির স্বাভাবিক চক্রের অংশ। তাই বুঝেশুনে অর্থব্যবস্থা পরিচালনা করা এবং সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।